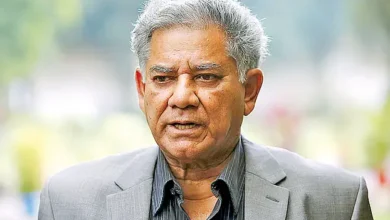পণ্যের দাম কেন বাড়ে? চার-পাঁচ হাত বদল

বাংলাদেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের দাম বাড়ার ঘটনা নতুন কিছু নয়। তবে মূল্যবৃদ্ধির পেছনের কারণ নিয়ে সাম্প্রতিক এক জরিপে উঠে এসেছে বিস্ময়কর তথ্য। সরবরাহ ঘাটতি ও উৎপাদন খরচ বৃদ্ধির পাশাপাশি সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখছে মধ্যস্বত্বভোগীদের অতিমুনাফা। মাঠ থেকে ভোক্তার হাতে পৌঁছাতে গিয়ে পণ্য বদলাচ্ছে চার-পাঁচবার মালিকানা, আর এর খেসারত দিতে হচ্ছে সাধারণ ক্রেতাকে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের করা জরিপ অনুযায়ী, চাল, আলু, পেঁয়াজ, ডিম ও ব্রয়লার মুরগির মতো পাঁচটি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বাড়ার পেছনে রয়েছে একাধিক কারণ। এই পণ্যের দাম উৎপাদন খরচের তুলনায় দ্বিগুণ বা তারও বেশি হয়ে যায়, যার ফলে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন কৃষক এবং সাধারণ মানুষ।
চাল: উৎপাদন খরচ ৩৪ টাকা, বিক্রি ৬৩ টাকায়!
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, বর্তমানে প্রতি কেজি মোটা চালের উৎপাদন খরচ প্রায় ৩৪ টাকা হলেও, খুচরা বাজারে সেটি বিক্রি হচ্ছে ৬২–৬৩ টাকায়। অর্থাৎ, উৎপাদন ব্যয়ের প্রায় দ্বিগুণ দামে চাল কিনতে বাধ্য হচ্ছেন ক্রেতারা। কারণ হিসেবে উঠে এসেছে উৎপাদক থেকে ভোক্তা পর্যন্ত পাঁচ-ছয়টি স্তর পেরিয়ে পৌঁছানোর বিষয়টি। প্রতিটি স্তরে কিছু না কিছু মুনাফা যোগ হয়, যা শেষপর্যন্ত চূড়ান্ত দামে প্রতিফলিত হয়।
চালের দাম বাড়ার পেছনে আরও কিছু কাঠামোগত কারণ রয়েছে। গত বছর অতিবৃষ্টি ও পোকার আক্রমণে আমন ধানের উৎপাদন কমে যায়। একই সময়ে ডলার সংকটে আমদানিও বাধাগ্রস্ত হয়। পাশাপাশি কৃষিজমি কমে যাওয়া, বিদ্যুৎ, সার, ডিজেল, মজুরি ও ব্যাংক সুদের হার বৃদ্ধিও চালের দামে প্রভাব ফেলেছে।
আলু: উৎপাদন ১ কোটি টন, দাম ৯০ টাকা!
বাংলাদেশে বছরে আলুর চাহিদা ৯০ লাখ টনের মতো, আর উৎপাদন হয় প্রায় ১ কোটি ৬ লাখ টন। অর্থাৎ উৎপাদন অতিরিক্ত হলেও দাম বাড়ছে। গত বছরের নভেম্বরে আলুর দাম কিছু এলাকায় কেজিপ্রতি ৯০ টাকায় পৌঁছায়। অথচ কৃষক সেই আলু বিক্রি করেছেন ১৮–৩৫ টাকায়, যার উৎপাদন খরচ ছিল মাত্র ১৭ টাকা।
দাম বাড়ার কারণ হিসেবে উঠে এসেছে তথ্যের গরমিল, সরবরাহ ব্যবস্থার দুর্বলতা, এবং হিমাগারে মজুত রেখে কৃত্রিম সংকট তৈরি। বিশেষত, হিমাগার থেকে আলু ছাড়ার সময় মূল্যবিভ্রান্তি সৃষ্টি করে বেশি লাভ আদায় করছেন কিছু ব্যবসায়ী। বাংলাদেশ ব্যাংক এ সমস্যা সমাধানে সুনির্দিষ্ট তথ্যভিত্তিক পরিকল্পনা ও ধাপে ধাপে আলু ছাড়ার প্রক্রিয়া চালু করার পরামর্শ দিয়েছে।
পেঁয়াজ: উৎপাদনে লোকসানেও বাড়ছে বাজারদর
২০২৩ সালের ডিসেম্বরে পেঁয়াজের দাম ইতিহাসের সর্বোচ্চ ২৫০ টাকা কেজিতে পৌঁছেছিল। এর পেছনে অতিবৃষ্টি ও বন্যার কারণে ব্যাপক পেঁয়াজ নষ্ট হওয়াকে দায়ী করা হয়েছে। পাশাপাশি কৃষক ও মধ্যস্বত্বভোগীদের একাংশ পরিকল্পিতভাবে মজুত করে বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করেছে বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে।
চলতি বছর পেঁয়াজের উৎপাদন বেড়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, মুড়িকাটা পেঁয়াজের প্রতি কেজির উৎপাদন খরচ ছিল ৫৪ টাকা। অথচ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে কৃষক সেটি বিক্রি করেছেন মাত্র ৩৫–৪৮ টাকায়। এতে কৃষকেরা গত বছরের তুলনায় এবার ২৪ শতাংশ লোকসানে পড়েছেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, গত বছরের অস্বাভাবিক লাভ দেখে অনেক কৃষক অতিরিক্ত পেঁয়াজ চাষ করেছেন, ফলে উৎপাদন বেড়ে গিয়ে দাম পড়ে গেছে।
ডিম ও ব্রয়লার: খাদ্যের দামেই উঠানামা
ডিম ও ব্রয়লার মুরগির দাম বাড়ার পেছনে বড় ভূমিকা রাখছে পোলট্রি খাদ্য ও মুরগির বাচ্চার মূল্য। জরিপ অনুযায়ী, ডিম উৎপাদনে খরচের ৭৪ শতাংশ এবং ব্রয়লার উৎপাদনে ৬৫ শতাংশই খরচ হয় খাদ্যের পেছনে। বাচ্চা কিনতেও খরচ হয় ১৪–২০ শতাংশ পর্যন্ত।
এই খাদ্য ও কাঁচামালের প্রায় ৭০ শতাংশ আমদানি নির্ভর হওয়ায় আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বাড়লে সরাসরি প্রভাব পড়ে দেশের খামারিদের ওপর। অনেক ছোট খামার মালিক এই অতিরিক্ত খরচ সামলাতে না পেরে উৎপাদন কমিয়ে দিয়েছেন বা খামার বন্ধ করে দিয়েছেন।
বাংলাদেশ ব্যাংক এই সংকট মোকাবিলায় পোলট্রি খাদ্য ও বাচ্চার দাম নিয়ন্ত্রণে আনা, এবং ছোট ও মাঝারি খামারিদের সহজ শর্তে ঋণ দেওয়ার সুপারিশ করেছে।
উৎপাদক নয়, লাভ পাচ্ছে মধ্যস্বত্বভোগী
সার্বিকভাবে বলা যায়, কৃষিপণ্যের বাজারে দাম বাড়লেও প্রকৃত লাভবান হচ্ছে না কৃষক। বরং উৎপাদন ব্যয় বহন করে শেষপর্যন্ত লোকসান গুনতে হয় তাঁদের। অন্যদিকে, মাঠ থেকে খুচরা বাজার পর্যন্ত যেসব মধ্যস্বত্বভোগী রয়েছেন, তারাই পাচ্ছেন লাভের বড় অংশ।
বাংলাদেশ ব্যাংকের মতে, প্রতিটি স্তরে নিয়ন্ত্রণ, তথ্যের স্বচ্ছতা, এবং পণ্যের ট্র্যাকিং সিস্টেম চালু করা না গেলে এই সমস্যা নিরসন সম্ভব নয়। বিশেষ করে কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে হবে এবং সরবরাহব্যবস্থাকে আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর করতে হবে।
নীতিগত সুপারিশ
বাংলাদেশ ব্যাংকের সুপারিশে বলা হয়েছে—
- অ-মৌসুমি সময়ে আমদানি উৎসাহিত করা ও শুল্ক কমানো, যাতে সরবরাহ ঘাটতি কমে।
- হিমাগার থেকে আলু ধাপে ধাপে ছাড়, এবং প্রতি মাসে দামের সীমা নির্ধারণ।
- পোলট্রি খাতকে সহজ শর্তে অর্থায়ন করে ক্ষুদ্র খামারিদের টিকিয়ে রাখা।
- উৎপাদন ও চাহিদার নির্ভুল তথ্যভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ।
বাংলাদেশের নিত্যপণ্যের বাজারে অস্থিরতা নতুন নয়, তবে তার পেছনের কাঠামোগত দুর্বলতা, নিয়ন্ত্রণহীন মধ্যস্বত্বভোগীদের ভূমিকা এবং উৎপাদন ব্যবস্থার দুর্বলতাগুলো এখন স্পষ্টভাবে চিহ্নিত হয়েছে। কৃষক যাতে প্রকৃত লাভবান হন এবং ভোক্তা ন্যায্য দামে পণ্য কিনতে পারেন—এই লক্ষ্যে নীতিনির্ধারকদের জরুরি পদক্ষেপ নেওয়া এখন সময়ের দাবি।