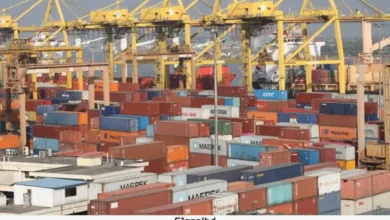বাংলাদেশে সাম্প্রতিক ডলার সংকট ও বৈদেশিক আর্থিক সম্পর্কের টানাপোড়েনের প্রভাব পড়েছে দেশের বৈদেশিক ঋণ প্রবাহে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে (অক্টোবর-ডিসেম্বর) দেশে বৈদেশিক ঋণ কমেছে ৭৪ কোটি মার্কিন ডলার, যা এক ধরনের নতুন অর্থনৈতিক সংকেত বহন করে।
ডলার সংকটের পটভূমি
গত এক বছরেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশে ডলার সংকট চলমান। আমদানি ব্যয়, বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ এবং রপ্তানি ও রেমিট্যান্সে কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধির অভাবে এই সংকট দিন দিন ঘনীভূত হয়েছে। এর ফলে দেশের ব্যাংকগুলো তাদের বিদেশি করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকগুলোর সঙ্গে লেনদেন সীমিত করেছে। অনেক ক্ষেত্রে বিদেশি ব্যাংকগুলো দেশের কিছু ব্যাংকের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, কারণ মাসের পর মাস ধরে তাদের আমদানি দায়ের অর্থ ফেরত পাচ্ছে না।
এই পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে দেশের ব্যাংকগুলোর অফশোর ব্যাংকিং কার্যক্রমে মন্দাভাব দেখা দেয় এবং তারই সরাসরি প্রভাব পড়ে বৈদেশিক ঋণ গ্রহণে।
বৈদেশিক ঋণে পতনের পরিসংখ্যান
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, অক্টোবর-ডিসেম্বর প্রান্তিকে মোট বৈদেশিক ঋণ কমেছে ৭৪ কোটি ডলার। এর মধ্যে সরকারি খাতের ঋণ কমেছে ২১ কোটি ৪০ লাখ ডলার এবং বেসরকারি খাতে ঋণ কমেছে ৫২ কোটি ২০ লাখ ডলার।
বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বেসরকারি খাতে সবচেয়ে বড় পতন ঘটেছে বায়ার্স ক্রেডিট এ, যার পরিমাণ ৪৯ কোটি ৬০ লাখ ডলার কমেছে। বায়ার্স ক্রেডিট হলো এমন একটি ঋণপ্রকল্প যেখানে বিদেশি ব্যাংক আমদানিকারকের হয়ে পণ্য মূল্য পরিশোধ করে দেয় এবং আমদানিকারক নির্দিষ্ট মেয়াদে (সাধারণত ৬ মাসে) সুদসহ সেই অর্থ ফেরত দেয়।
বিদেশি ব্যাংকের আস্থা কমে যাচ্ছে?
বিশ্বব্যাপী উচ্চ সুদের হার, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও বাংলাদেশের আমদানি দায়ে বিলম্বের কারণে অনেক আন্তর্জাতিক ব্যাংক স্থানীয় ব্যাংকগুলোর ওপর আস্থা হারাচ্ছে। ফলে বিদেশি ব্যাংকগুলো এখন বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোর জন্য ডলার সীমা (Credit Limit) কমিয়ে দিয়েছে, এবং কিছু ব্যাংক তাদের করেসপন্ডেন্ট রিলেশনশিপ বাতিল করে ফেলেছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ডিসেম্বর ২০২৪ শেষে মোট বৈদেশিক ঋণের স্থিতি ছিল ১০ হাজার ৩৬৩ কোটি ডলার, যেখানে সেপ্টেম্বরে এই পরিমাণ ছিল ১০ হাজার ৪৩৭ কোটি ডলার। অর্থাৎ তিন মাসের ব্যবধানে ঋণ কমেছে ৭৪ কোটি ডলার।
সরকারি ও বেসরকারি খাতে ঋণের চিত্র
ডিসেম্বরের হিসাব অনুযায়ী:
- সরকার ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের ঋণ: ৮ হাজার ৪২১ কোটি ডলার
- বেসরকারি খাতের ঋণ: ১ হাজার ৯৪২ কোটি ডলার
তুলনামূলকভাবে সেপ্টেম্বর ২০২৪ প্রান্তিকে এই পরিমাণ ছিল:
- সরকার: ৮ হাজার ৪৪২ কোটি ডলার
- বেসরকারি খাত: ১ হাজার ৯৯৪ কোটি ডলার
এর মানে, সরকার ও বেসরকারি খাত উভয়ই বৈদেশিক ঋণ গ্রহণে পিছিয়ে গেছে, যা দেশের সামগ্রিক বিনিয়োগ এবং উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতিতে প্রভাব ফেলতে পারে।
দীর্ঘমেয়াদি বনাম স্বল্পমেয়াদি ঋণ
ডিসেম্বর প্রান্তিকে মোট ঋণের মধ্যে:
- দীর্ঘমেয়াদি ঋণ: ৯ হাজার ৬৯ কোটি ডলার
- স্বল্পমেয়াদি ঋণ: ১ হাজার ২৯৫ কোটি ডলার
এই তথ্য বলছে, দীর্ঘমেয়াদি ঋণই এখনো বৈদেশিক অর্থায়নের মূল ভিত্তি হয়ে আছে। তবে স্বল্পমেয়াদি ঋণের ওপর নির্ভরতা বাড়ানোর মাধ্যমে আমদানি খাতে মসৃণতা আনা যেত, যা বর্তমানে সংকুচিত হয়ে পড়েছে।
বিদেশি ঋণের দীর্ঘমেয়াদি প্রবণতা
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ডিসেম্বর ২০২৩ প্রান্তিকে বিদেশি ঋণের পরিমাণ ছিল ১০ হাজার ৬৪ কোটি ডলার। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে ঋণের পরিমাণ বেড়েছে প্রায় ৩০০ কোটি ডলার বা প্রায় ৩ শতাংশ।
২০০৬ সালে চারদলীয় জোট সরকার বিদায় নেওয়ার সময় দেশের বৈদেশিক ঋণ ছিল প্রায় ১ হাজার ৯০০ কোটি ডলার। ২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় শেষে এই ঋণ বেড়ে দাঁড়ায় ২ হাজার ১১৯ কোটি ডলারে। সেখান থেকে বর্তমান সময়ে প্রায় পাঁচগুণেরও বেশি ঋণ বেড়েছে।
২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ২০২৪ সালের জুলাই পর্যন্ত সময়ে বিদেশি ঋণের স্থিতি দাঁড়ায় ১০ হাজার ৩৭৯ কোটি ডলারে। সরকার প্রায় ৮৪ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করে বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্প, বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য।
বর্তমান প্রেক্ষাপটে চ্যালেঞ্জ
বর্তমানে রাজনৈতিক অস্থিরতা, বৈদেশিক আস্থার অভাব এবং আমদানি দায়ে অনিয়মিত পরিশোধ – এই তিনটি বড় কারণ বিদেশি ঋণের প্রবাহে হুমকি সৃষ্টি করছে। বিশেষ করে বেসরকারি খাতে বায়ার্স ক্রেডিট কমে যাওয়ায় আমদানি-নির্ভর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো পড়েছে বিপাকে। আবার সরকারি খাতেও ঋণ কমে যাওয়ায় অনেক অবকাঠামো প্রকল্প অর্থায়ন জটিলতায় পড়তে পারে।
করণীয় ও সুপারিশ
বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, বৈদেশিক ঋণ প্রবাহ স্বাভাবিক করতে হলে বাংলাদেশকে অবশ্যই নিচের বিষয়গুলো বিবেচনায় আনতে হবে:
- ডলার সংকট নিরসনে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যকর হস্তক্ষেপ
- বিদেশি ব্যাংকের আস্থা পুনরুদ্ধারে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা
- ঋণের অর্থ যথাযথভাবে ব্যবহারে নজরদারি বৃদ্ধি
- রপ্তানি ও রেমিট্যান্স বাড়াতে নীতিগত সংস্কার
- দীর্ঘমেয়াদে ঋণ নির্ভরতা কমিয়ে স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলা